বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিস্থিতি

- প্রকাশিত : শনিবার, ১ জুন, ২০২৪
- ২৩২ জন পড়েছেন

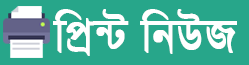
যেকোনো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাকে আমরা সাধারণত ইনভেস্টমেন্ট বলি। বিনিয়োগটা ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন খাতে করা হয়ে থাকে। ভৌত অবকাঠামোতে বিনিয়োগ হয়, স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ হয়, শিক্ষা খাতে হয়। এই বিনিয়োগটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
কারণ আমরা জানি, বিনিয়োগটা প্রবৃদ্ধি (গ্রোথ), কর্মসংস্থান এবং বিভিন্ন কিছুর সঙ্গে জড়িত। ইদানীং বিনিয়োগের বিষয়টা আরো সামনে চলে আসছে। আমরা এখন দেখছি, আমাদের অর্থের সংকুলান হচ্ছে না, অর্থের অভাব। ব্যাংকে তারল্য সংকট।
রিজার্ভ কমে যাচ্ছে। বৈদেশিক বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে। এফডিআই আসছে না। পোর্টফোলিও বিনিয়োগ খুবই কম।
সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বড় একটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছি।
এক টাকাটা এখন নয়, ধারাবাহিকভাবে পেতে থাকবে। অতএব ‘ফোর ইসটু ওয়ান রেশিও’ যদি হয়, যদি আমরা ৩০ থেকে ৩২-এ যেতে না পারি, তাহলে তো আমরা গ্রোথে ৭.৫ বা আটে যেতে পারব না। ‘ফোর ইসটু ওয়ান’ আমরা সাতে যেতে পারব, তার মধ্যে আবার লিকেজ আছে, সব বিনিয়োগ তো হয় না। বিনিয়োগ ওয়েস্টেজ হয়। বিনিয়োগ সঠিক জায়গায় যায় না। অতএব এখন যদি আমরা বিনিয়োগ না বাড়াই, তাহলে আমাদের জন্য ডিফিকাল্ট হবে।
 একটি দেশে বিনিয়োগ সাধারণত দুই ধরনের হয়। একটা হলো অভ্যন্তরীণ, আরেকটা হলো বৈদেশিক। অভ্যন্তরীণ উৎসর মধ্যে আছে আমাদের সঞ্চয়পত্র, সেভিংস সার্টিফিকেট, প্রাইজ বন্ডের মাধ্যমে, অভ্যন্তরীণভাবে ব্যাংকে টাকা-পয়সা রাখে যারা, যেসব ডিপোজিট ব্যাংক ক্রিয়েট করে, সেটা হলো আমাদের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের একটি উৎস। আমাদের বিদেশ থেকে কিছু বিনিয়োগ আসে, সেটা হলো ডলার বন্ড কেনে। ইনভেস্টমেন্ট বন্ড কেনে—আমাদের যারা বিদেশে আছে, তারা। এটা হলো আমাদের, যেটাকে আমরা বলতে পারি, ডমেস্টিক সোর্স তথা বাংলাদেশিদের পক্ষ থেকে বিনিয়োগের পরিমাণ।
একটি দেশে বিনিয়োগ সাধারণত দুই ধরনের হয়। একটা হলো অভ্যন্তরীণ, আরেকটা হলো বৈদেশিক। অভ্যন্তরীণ উৎসর মধ্যে আছে আমাদের সঞ্চয়পত্র, সেভিংস সার্টিফিকেট, প্রাইজ বন্ডের মাধ্যমে, অভ্যন্তরীণভাবে ব্যাংকে টাকা-পয়সা রাখে যারা, যেসব ডিপোজিট ব্যাংক ক্রিয়েট করে, সেটা হলো আমাদের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের একটি উৎস। আমাদের বিদেশ থেকে কিছু বিনিয়োগ আসে, সেটা হলো ডলার বন্ড কেনে। ইনভেস্টমেন্ট বন্ড কেনে—আমাদের যারা বিদেশে আছে, তারা। এটা হলো আমাদের, যেটাকে আমরা বলতে পারি, ডমেস্টিক সোর্স তথা বাংলাদেশিদের পক্ষ থেকে বিনিয়োগের পরিমাণ।
আরেকটা হলো বৈদেশিক বিনিয়োগ। সেটার একটা হলো ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট (এফবিআই)। বহু বিদেশি কম্পানি বিনিয়োগ করে। তাদের বিভিন্ন কম্পানির মাধ্যমে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের (ব্যাংকসহ) মাধ্যমে। আরেকটা হলো ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট; সেটা হলো শেয়ার মার্কেটে। যেমন—আমাদের নাগরিক বিভিন্ন কম্পানির শেয়ার কেনে। সেখানে বাইরের লোকও কিছু শেয়ার কেনে। বৈদেশিক বিনিয়োগের দিক সেদিক দিয়ে আমরা এখনো পিছিয়ে আছি।
বিনিয়োগের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং ব্যবসার পরিস্থিতি। যেমন—২০২০ সালে গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স বলে একটা রিপোর্টে আছে, যেখানে ১৩০ দেশে কী কী সুবিধা আছে, তা বলা আছে। সেখানে দেখা গেছে, সবচেয়ে শীর্ষে সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, ইউএস ইউকে আছে। আমাদের আশপাশের মধ্যে ইন্ডিয়া একটা বিরাট বিনিয়োগের কেন্দ্র। ইন্ডিয়ার ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট বেশ বেশি। এমনকি ইন্ডিয়ারটা এখন শেয়ার মার্কেটে ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে; মুম্বাইয়ের শেয়ার মার্কেটের ক্যাপিটাল। তারপর সাউথ আফ্রিকা আছে, সিঙ্গাপুর আছে, ভিয়েতনাম আছে। এদিকে চীন তো আছেই। এই ক্যাটাগরিতে ১৩০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান হলো ১২৪। চিন্তার বিষয়! ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন সেটা প্রকাশ করছে।
আমাদের দুর্বলতা কোথায়? আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা আছে। রাজনৈতিক ইস্যু আছে। নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার দুর্বলতা আছে। বিজনেস এনভায়রনমেন্ট, যাকে বলে ডুয়িং বিজনেস, ব্যবসা করার যে সুবিধা, সেটা আমাদের সন্তোষজনক নয়। আরেকটা দুর্বলতা আমাদের হিউম্যান ক্যাপিটাল কম। স্কিল ট্রেনিং বাংলাদেশে অনেক কম। হিউম্যান ক্যাপিটালে ১৩০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১২৯। কিন্তু ওদিকে আবার ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা ভৌত অবকাঠামো ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভালো—৯২। কিন্তু হিউম্যান ক্যাপিটাল ও ইনোভেশনে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে।
দক্ষতা এবং চাকরির ব্যাপারে বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে এডিবি ২০২০ সালে একটি রিপোর্ট বের করেছিল। সেখানে বলা হয়েছিল যে বাংলাদেশের এডুকেশন লেভেল লো, কোয়ালিটি ভালো নয়, স্কিল লেভেল লো, শ্রমিকদের দক্ষতা অনেক কম। জাপানের এশিয়ান প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন বলেছে, বাংলাদেশের লেবার প্রডাক্টিভিটি কম। আমরা যে গার্মেন্টসে দেখি বা বিভিন্ন জায়গায় দেখি, অন্য দেশে মজুরি বেশি দেয়। কারণ প্রডাক্টিভিটি উঁচু। যারা মজুরি বেশি পায়, তাদের দক্ষতা বেশি। আমাদের এখানে দ্বিমুখী সমস্যা। একটি হলো, আমাদের শ্রমিকদের বেতন কম এবং তাদের থাকা-খাওয়ার আবহ ভালো নয়। সুতরাং তারা এর চেয়ে বেশি কী দক্ষ হবে? দক্ষতা বাড়ালে মজুরি বাড়াতে হবে। মজুরি বাড়াতে হলে খরচ বেড়ে যাবে। প্রডাক্টিভিটি বাড়াতে হলে টাকা-পয়সা খরচ করতে হবে।
এডিবির রিপোর্টে ওরা বলেছে, এই যে আমাদের বড় কম্পানিগুলোর ২৫ শতাংশের বেশি প্রশিক্ষণের ব্যাপারে মোটেও উৎসাহী নয়। এই যে বড় বড় কম্পানি আছে দেশে, তারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ট্রেনিংয়ের ব্যাপারে সামান্যও ভাবে না। সম্প্রতি দেখলাম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিনিয়োগের ব্যাপারে প্রচুর কথা বলেছেন। এটা সঠিক, বিনিয়োগটা না বাড়ালে তথা বৈদেশিক বিনিয়োগ না এলে তো রিজার্ভও বাড়বে না।
এখন কী করতে হবে? সামনের দিকে যেতে হলে কী করার আগে কী প্রয়োজন? যেটাকে আমরা বলি ইনভেস্টমেন্ট এনভায়রনমেন্ট—বিনিয়োগের আবহ তৈরি করতে হবে। এর জন্য আমি পাঁচটি জিনিসের ওপর জোর দিচ্ছি। এক. আইন। আমাদের কম্পানি আইন বলুন, কম্পিটিশন ল বলুন, মজুদদারি আইন বলুন—বেশির ভাগই মোটামুটি কাগজে-কলমে ভালো। কিন্তু এগুলোর প্রয়োগ দুর্বল। এ জন্য বাইরে থেকে কম্পানি যারা আসে, তারা ভয় পায়। আইনের আওতায় কোর্টে যাবে, এডিআর করবে—কোর্টে তো দীর্ঘসূত্রতা। কত কম্পানির মামলা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কোর্টে ঝুলে আছে। ব্যবসায়ীরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হন।
আরেকটা জিনিস হলো ল্যান্ড রেজিস্ট্রেশন আইন। বাইরে থেকে যারা আসে, তারা যখন ল্যান্ড রেজিস্ট্রেশন করতে যায় বা কোনো কিছু রেজিস্ট্রেশন করতে যায়, কত রকম ঝুঁকি পোহাতে হয়। কত রকম দুর্নীতি। কত রকম কাগজপত্র, কত জায়গায় যেতে হয়। এটা তো অকল্পনীয়। সম্প্রতি সরকার কতগুলো স্পেশাল ইকোনমিক জোন করেছে। কিন্তু অনেকগুলো স্পেশাল ইকোনমিক জোন মুখ থুবড়ে আছে। সেগুলো খুব বেশি ভালো করতে পারছে না। কয়েকটা ভালো করেছে। আইন বিষয়টা সবচেয়ে জরুরি। এমনকি কম্পানি আইন, ব্যাংক কম্পানি আইনে সার্বিকভাবে অনেক দুর্বলতা আছে।
দুই. নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ। এখানে বাংলাদেশ ব্যাংক আছে, সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন আছে, এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আছে—এগুলোকে আমরা বলি রেগুলেটরি বডি—নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা। এদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনের উন্নতি করতে হবে। ব্যাংকিং অবস্থা কী, পুঁজিবাজারের অবস্থা কী? কোনো এনার্জি পলিসি নেই। একদিন এটার দাম বাড়ায়, অন্য দিন আরেকটার দাম বাড়ায়। কমে না। পেট্রলের দাম বাড়ায়, গ্যাসের দাম বাড়ায়। এদিকে আবার যা ভালো আইনকানুন আছে, সেগুলোর প্রয়োগ নেই।
তিন. প্রমোটিং বডি তথা ব্যবসা সহায়তাকারী সংস্থা। এখানে বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা), এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো আছে, বাংলাদেশ রপ্তানি অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা) আছে—তারা ব্যবসা-বাণিজ্য সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান। ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান এখানে আছে, যারা প্রমোটিং বডি। তাদের অবস্থা কেমন? প্রথম সরকারি যেসব সহায়তাকারী সংস্থা আছে, তাদের পারফরম্যান্স কেমন? খুব ভালো নয়। আর যদি ব্যাংক ফিন্যানশিয়াল ইনস্টিটিশন ধরি, সেখানকার অবস্থাও খারাপ। ব্যবসায়ীরা কোথায় যাবেন? তাঁদের তো সাপোর্ট লাগবে। বিদেশিরা কার কাছে যাবে? কিভাবে সহায়তা পাবে? আগেই আমি বলেছি যে যথাযথ স্থানে দক্ষ লোকের অভাব। ইনোভেশনের অভাব। এডুকেশন কম বা দুর্বল। তবে বাইরে থেকে লোকজন টাকা-পয়সা দিয়ে তো বিপদে পড়বে।
চার. গুড গভর্ন্যান্স। স্বচ্ছতা, জবাবদিহি নেই। যেখানে যাওয়া হয়, সেখানেই টাকা-পয়সার লেনদেন ছাড়া কিছুই হয় না। যাদের টাকা-পয়সা আছে, যারা ক্ষমতার কাছাকাছি যেতে পারে, যাদের আমলাতান্ত্রিক যোগাযোগ আছে; তারা ব্যবসা পাবে, বাকিরা পাবে না। যত ইনোভেশনই হোক। এখানে একটি উদাহরণ দিই, অনেক উদ্যোক্তা আছে, যাদের ইকুয়িটি ফিন্যান্স দরকার, অনেক তরুণ ছোট ছোট আইটি ইন্ডাস্ট্রি করে, সেখানে তাদের ইকুয়িটি ফিন্যান্স দরকার। তাদের ১০ লাখ টাকা লাগলে কেউ তিন লাখ টাকা দিয়ে তাদের সঙ্গে অংশীদার হতে পারে। ইকুয়িটি ফিন্যান্সিং, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বা স্টার্ট আপ ফান্ড—এগুলোর তো অবস্থা খারাপ বাংলাদেশে। কিছু হয়েছে। সৃজনশীল উদ্যোক্তা যারা, তাদের তো তেমন সুযোগ নেই। তাদের জন্য যে আবহ দরকার, যে সহযোগিতা দরকার, সেগুলো বাংলাদেশে নেই। এই আমরা বলছি, তরুণরা এগিয়ে আসবে, নবীন উদ্যোক্তারা ব্যবসা করবে—সবার তো চাকরি করার প্রয়োজন নেই, সবাইকে তো চাকরি দেওয়া সম্ভবও নয়—এদিকে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি।
পাঁচ. করাপশন তথা দুর্নীতি। দুর্নীতি যদি দূর করা না যায়, তবে কোনো কিছুই করা যাবে না এখানে। এফিশিয়েন্সি বাড়ানো যাবে না। প্রডাক্টিভিটি বাড়ানো যাবে না। লভ্যাংশ বাড়ানো যাবে না। সব খেয়ে ফেলবে দুর্নীতি। সৃজনশীল বা উদ্যোগী লোকজন নতুন ধ্যান-ধারণা নিয়ে ব্যবসায় আসবে—এটা সম্ভব হবে না। দুর্নীতির সবচেয়ে বড় খারাপ বিষয় হলো মানি লন্ডারিং। দুর্নীতির টাকা বেশির ভাগ পাচার হয়ে যায়। কষ্টের টাকা তো কেউ পাচার করবে না। এটা মানুষ সঠিকভাবে ভোগ করতে চায়। বৈধভাবে ব্যবহার করতে চায়। বাইরে নিলে বৈধভাবে নিতে চায়। দুর্নীতির টাকা তো পাচার হয়ে যায়। মানি লন্ডারিং, করাপশন রুখতে না পারলে দেশের দ্রুত উন্নয়ন হবে না। বিনিয়োগ বাড়বে না। অতএব সামনে যেতে হলে এই জিনিসগুলো আমাদের বিবেচনা করতেই হবে।
সব শেষে কয়েকটা জিনিস দরকার। প্রথমত, আমাদের বাজেটে, পলিসিতে এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইনভেস্টমেন্টটা আমরা প্রায়োরিটি দেব। প্রডাক্টিভিটি বাড়াব, যাতে লোকজনের কর্মসংস্থান হয়। অপ্রয়োজনীয় মেগাপ্রজেক্ট, লোক-দেখানো প্রজেক্টে ইনভেস্ট করা যাবে না। মোদ্দাকথা, বিনিয়োগের মাধ্যমে অপচয় বা অপচয়ের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করা ঠিক হবে না।
দ্বিতীয়ত, আমাদের যেসব ট্যাক্স আইন আছে, প্রণোদনা আছে, বিভিন্ন রকম ব্যাংক থেকে লোন, ফান্ড—এগুলো খুব সাবধানতার সঙ্গে দিতে হবে। কোন বিনিয়োগটা আমাদের জন্য ভালো, কোন বিনিয়োগটা আমাদের জন্য প্রফিটেবল, কোন বিনিয়োগটা সার্বিকভাবে বাংলাদেশের জনগণের ব্যাবসায়িক উন্নতি হবে, জনগণের উন্নতি হবে—সেটা দেখতে হবে।
তৃতীয়ত, আমাদের নলেজ বেজড ইকোনমি, স্কিল বেজড ইকোনমি তথা বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও দক্ষতা ভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য-প্রডাকশন—এগুলোর দিকে যেতে হবে। এগুলো যদি না করি, আধুনিক স্কিল, প্রযুক্তি ও দক্ষতা ভিত্তিক ব্যবসা যদি আমরা না করি, তাহলে এগিয়ে যেতে পারব না। যেসব দেশ এগিয়ে গেছে, তারা এসব জিনিসের ওপর নজর বেশি দিয়েছে।
লেখক : সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়









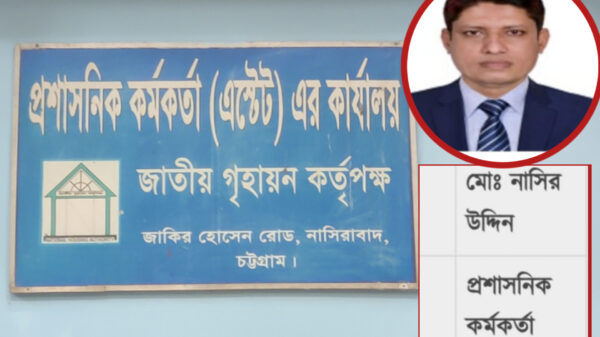










Leave a Reply